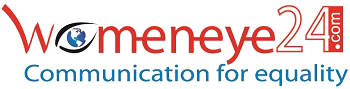সাংবাদিক সোহেল সানি। ছবি-উইমেনআই
‘সুস্থ সাংস্কৃতিক পদক্ষেপ স্বাধীনতাকে করে সংহত আর অসুস্থ অপসংস্কৃতি স্বাধীনতাকে করে সংহার।’
উপর্যুক্ত কথাটি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ফ্রেডরিক এঞ্জেলসের। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এরকম বিশ্বাস থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের সংযোগ ঘটিয়ে ছিলেন ছাত্র অবস্থায়ই।
বঙ্গবন্ধু হত্যাত্তোর আমাদের মুক্তিসংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতভাষ্য স্বাধীনতাকে সংহার করতে এতটাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো, যা ভাবতে গিয়ে আমাকে ফ্রেডরিক এঞ্জেলসের ওই উক্তিটিকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে। বাঙালির ১৯৪৮ এর ভাষা সংগ্রাম ও ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ, তার সাফল্যের ক্ষেত্রে নিরন্তর ভুমিকা রেখেছে, আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনও।
শেখ মুজিবুর রহমান সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রামের দিকেও যে দৃষ্টি রাখতেন, তার প্রমাণ আমরা তাঁর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তৎপরতায়ও দেখতে পাই। পরবর্তীতে শেখ মুজিবের অনুসারীরাও মুক্তিযুদ্ধে সংস্কৃতির দাহ্যগুণ উপলব্ধি করেছিলেন। স্বাধীনতার পক্ষে যে লৌহদৃঢ় ঐক্য গড়ে ওঠে তাতে সংস্কৃতির অবদান অসামান্য। শেখ মুজিব রবীন্দ্র-নজরুলকে হৃদয়ে ধারণ করতেন বলেই স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশের। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে গিরিডিতে বসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেন - বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি- তুমি অপরূপে বাহির হলে জননী'..
আর কবি নজরুল ১৯২০ সালে লিখেন 'বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধ আর তারও আগে কবিতায় ব্যবহার করেন 'জয়বাংলা' কথাটি।
শেখ মুজিব রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনটাকেও এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা ঘটনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি ইতিহাসের তথ্যউপাত্ত হাজির করে।
১৯৬৭ সাল। লৌহমানব খ্যাত পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ফিল্ডমার্শাল আইউব খান রাষ্ট্রীয়ভাবে 'রবীন্দ্র সংগীত' নিষিদ্ধ করেন, তখন বিচলিত হয়ে হয়ে পড়েন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির মুক্তির সনদ '৬ দফা' নিয়ে তখন তাঁর কর্মব্যস্ততা। কিন্তু এর মধ্যেও তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একটি বড়সড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন নেপথ্যে থেকে। তিনি জগন্নাথ কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অজিত কুমার গুহকে দিয়ে। জগন্নাথ কলেজ চত্বরে অন্তত দশ হাজার শ্রোতামণ্ডলির উপস্থিতি ছিল সেই অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া হবে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এটা ভাবতেও পারছিলেন না - শ্রোতারা। কিন্তু তাই ঘটলো -
নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল ছিন্ন করে অনুষ্ঠানে আকস্মিকভাবে গাওয়া হলো রবীন্দ্র সংগীত। এ খবর চলে গেলো সরকারি মহলে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান। জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাইদুর রহমানকে প্রত্যাহার করলেন। অধ্যাপক অজিত গুহকে বিতাড়িত করলেন কলেজ থেকেই।পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণগ্রহণে জগন্নাথ কলেজকে সরকারিকরণ করে ফেললেন।
রবীন্দ্রভক্ত মুজিব বিভিন্ন বক্তৃতায় ‘কবিগুরু’ সম্বোধন করে কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করতেন। আন্দোলন প্রশ্নে সমমনাদের সঙ্গে বনিবনা না হলেই বক্তৃতায় জুড়ে দিতেন কবিগুরুর সেই বিখ্যাত সঙ্গীতের পংক্তি ‘কেউ যদি তোর ডাক শুনে না আসে , তবে একলা চলে...রে’। স্বদেশে ফিরে তিনি রেসকোর্স ময়দানের গণসমুদ্রে আবেগঘন ভাষণে কবিগুরুর 'বাঙালি করেছো মোদের মানুষ করোনি' পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- কবিগুরু তুমি দেখে যাও বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা- আমি তোমায় ভালোবাসি" এবং বিদ্রোহী কবি নজরুলের ‘চল চল চল ঊর্দ্ধ গগনে ..’ কবিতাটিকে রণ সঙ্গীত হিসাবে অনুমোদন করেন।
১৯৭৩ সালে অসুস্থ ও নির্বাক কবি নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে এনে জাতীয় কবির মর্যাদায় আসীন করেন।
মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘জয়বাংলা" শ্লোগানটি শেখ মুজিব ছাত্র অবস্থায় আত্মস্থ করেন কবি নজরুলের মুখে শুনে।
বঙ্গবন্ধু হত্যার পর জয়বাংলা শ্লোগানটিকেও নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে ক্ষমতায় এসেই রাষ্ট্রীয় শ্লোগান হিসাবে গ্রহণ করতে বহুবছর পার করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত গণমাধ্যমে দুচারদিন আগেও যখন শুনতে পাই জয়বাংলা শ্লোগান দেয়ার অপরাধে নাটোরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাসুদুর রহমান চাকুরিচ্যুত হন এবং তা আবার একজন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুছের নির্দেশে - তখন হৃদয়ে বড্ড রক্তক্ষরণ হয়। যাহোক জয়বাংলা কথাটির উৎস সম্পর্কে বলছি। কবি নজরুল বৃটিশবিরোধী আন্দোলন চলাকালে মাদারীপুরে যান। কারামুক্ত চরমপন্থী নেতা পূর্ণচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায়। কবি তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি কবিতায় জয়বাংলা শব্দটি ব্যবহার করেন। ওই সভায় উপস্থিত শেখ মুজিব তখনই 'জয়বাংলা' কথাটিকে আত্মস্থ করেন। বাঙালি জাতির দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্র-নজরুল দুই বরেণ্য কবিরই স্বপ্ন ছিলো অখণ্ড বাংলাকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ ‘আমার সোনার বাংলা’ সংগীতটি রচনা করেন ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে। স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা অবিভক্ত বাংলার রাজধানী তথা ভারতেরও রাজধানী কলকাতায় 'বঙ্গভবন' নামে একটি ভবনের ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করা হয় রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখনো নোবেল প্রাইজ অর্জন করেননি। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির এক বছর পরই ১৯১২ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আইন পাস হয়ে বাংলা আবারও এক হয়। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ছুরি চালিয়ে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবারও দ্বিখণ্ডিত হয়। এর সাত বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ ঘটে। বিদ্রোহী কবি নজরুলও রবীন্দ্রনাথের মতো অখন্ড বাংলায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু নজরুলও ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই থেকে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। হারান স্মরণশক্তি।
'বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপররূপে বাহির হলে জননী'। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে গিরিডিতে বসে এই মধুর সঙ্গীতটি রচনা করেন। এরপরই কবি নজরুল রচনা করেন 'বাংলাদেশ' নামক প্রবন্ধটি।
১৯৪২ সালের ১০ জুলাই থেকে।
বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ নামটি দুই প্রিয় কবির লেখা পড়েই মনে আত্মস্থ করেছিলেন। রবীন্দ্র-নজরুলের পূর্ববাংলায় বসতি স্থাপন করলেও জন্মটা পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলা রাষ্ট্র নয়, পরাধীন রাজ্য বা ভারতের প্রদেশ মাত্র। দুই কবি বেঁচে থাকলে বাংলা দুই টুকরো করা সম্ভব হতো কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ইদানিং জয়বাংলা শ্লোগান ব্যবহার করায় ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতারা বলছেন মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম বাংলাকে যুক্ত করতে ষড়যন্ত্র করছেন। ১৯৫৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা পশ্চিম বাংলায় সংর্বধনা সভায় যোগ দিয়ে বলেছিলেন - 'বাংলা অবিভাজ্য। একে ভাঙ্গা যায়না। দেশবিভাগের নামে দুই বাংলার মধ্যে এক মিথ্যার প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে।'
সেদিন ছিলো উল্টো অভিযোগ। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী এবং গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ শেরেবাংলাকে দেশদ্রোহী বলেন। পূর্ববাংলাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত - এমন অভিযোগ এনে শেরেবাংলা সরকারকেই বরখাস্ত করে দেন। ভারতের লেলিয়ে দেয়া কুকুর আখ্যা দিয়ে খোদ পাকিস্তান প্রস্তাবক সোহরাওয়ার্দীর গণপরিষদ সদস্য পদই কেড়ে নিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান।
পূর্ববাংলার ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে সেই রবীন্দ্র নজরুলের বাংলাদেশবঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা অর্জন করোছে।
১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিব ‘পূর্ববাংলার’ নাম ‘পূর্বপাকিস্তান’ রাখার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, "The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own.
তিনি পূর্ববাংলা- পূর্ববঙ্গও বা পূর্ব পাকিস্তানও নয় বাংলাদেশ রাখার দাবি জানান।
প্রসঙ্গত, শেখ মুজিব যাঁকে লিডার বলে সম্মোধন করতেন, সেই গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই তখন গণপরিষদ নেতা হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রের ন্যায় পূর্বপাকিস্তানেও তখন আওয়ামী লীগ সরকারে।
সেদিন শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষেই কেবল সম্ভব হয় পূর্ববাংলার নাম বাংলা অথবা বাংলাদেশ রাখার দাবি তোলা।
টাঙ্গাইলের কাগমারী সম্মেলনের সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছিল বিরাট এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৯৫৭ সালের ৮-৯-১০ ফেব্রুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মিশর, জাপান, ভারত থেকে খ্যাতনামা শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এতে অংশ নেন।
সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, কাগমারী সম্মেলন বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং তার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক ভিত্তি-ভূমি নির্মাণের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার অন্যতম।
১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, আমরা হিন্দু মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তবতা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা লুঙ্গি-টুপি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।
মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ-সুকান্তের সমান্তরাল ব্যবহার ছিল চমৎকার শিক্ষা। বঙ্গবন্ধু তাঁর বন্ধু প্রখ্যাত শিল্পী কলিম শরাফীকে বলেন, ‘শিল্পকলা একাডেমি করে দিলাম, লোকশিল্পসহ শিল্পকর্মের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা করো। ’
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট ও ইতিহাস গবেষক।
//জ//