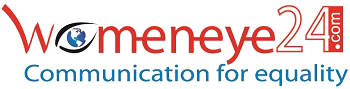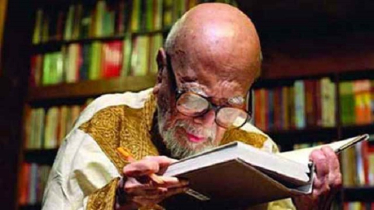মলয় চন্দন মুখোপাধ্যায়:
শঙ্করাচার্যের একটি ধ্রবপদ শিরোধার্য হয়ে আছে আমার যৌবনকাল থেকে, - ক্ষণমিহসজ্জনসঙ্গতিরেকা/ ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা। ' অর্থাৎ, জীবনে যদি মুহূর্তের জন্য- ও সজ্জনের সঙ্গলাভ করা যায়, জীবনের পরপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটাই তরণী , কিনা নৌকোর কাজ করবে। সেই মহান বাক্য আমাকে সর্বত্র মহান মানুষের সান্নিধ্য পেতে প্রলুব্ধ করে। আমার দেশে, বাংলাদেশে।
এখন আমি বাংলাদেশের এমন কয়েকজনের কথা বলবো,যাঁদের সান্নিধ্য ও অপার স্নেহ - ভালোবাসা আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।
আহমদ শরীফ। তাঁর সঙ্গে আলাপের আগে তাঁর লেখা পড়েছি এবং ব্যক্তিমানুষ হিশেবে তাঁর অসাধারণত্বের কথা শুনেছি ( প্রথমা রায়মণ্ডলকে তিনি উদারচিত্তে নিজের কন্যা জ্ঞান করতেন, শুনেছি )।
তাঁর ধানমন্ডির বাসায় প্রতি শুক্রবারের আড্ডায় ছাত্র শিক্ষক রাজনীতিবিদ মুক্তিযোদ্ধা মিলিটারির লোক , বিচিত্র বয়স ও পেশার মানুষকে দেখেছি। মাঝেমাঝে মতান্তরে উত্তপ্ত হয়ে উঠতো গৃহ। তিনি হাততালি দিয়ে থামাতেন। তাঁকে সাহিত্য রাজনীতি সমাজ ও অর্থনীতি আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তিনি সবকিছু বুঝিয়ে দিতেন। তখন অবসরে তিনি , বয়স সত্তরোর্ধে। মৌলবাদীদের আক্রমণ আশঙ্কায় তাঁর ঘরে পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা নিতে চেয়েছিল সরকার। তিনি রাজি হন নি এই বলে যে তিনি এমন কোনো কেউকেটা নন যে তাঁর জীবনকে এতো মূল্যবান মনে করেন।
প্রত্যেক অতিথিকে চা - নাস্তা দিতেন নিজ হাতে। এমনটা শান্তিনিকেতনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যয়ের মধ্যেও দেখেছি। অতিথিকে সম্মান জানানোর এই মহত্ত্বের কাছে নতজানু না হয়ে পারি নি। মরণোত্তর চোখ ও দেহদান করে তিনি আমার কাছে পরম শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন।
শামসুর রাহমানের মধ্যে পেয়েছি একদিকে পরিশীলিত মন , অন্যদিকে কবিসুলভ উদার- উদাসীন - মায়াময় চোখ। তাঁর পোষাকে আভিজাত্য ছিল , ধীর লয়ের কথাবার্তায় থাকতো নিবিড় সুধা , আর তাঁর হাসিটি ছিল সন্তচিহ্নিত। তাঁর স্বকণ্ঠে কবিতাপাঠ শুনেছি , আমাকে তিনি তাঁর লেখা প্রায় সব বই উপহার দিয়েছেন , বাসায় আমন্ত্রণ করে খাইয়েছেন। তাঁকে নিয়ে একাধিক লেখায় তাঁর প্রতি মুগ্ধতা, তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা আছে আমার। নিয়েছি তাঁর সাক্ষাৎকার। ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিয়েছি তাঁর সঙ্গে 'দৈনিক বাংলা' অফিসে, এবং কলকাতায় । আলোচনার বিষয় কখনো পরলোক , কখনো নারীর সৌন্দর্য , কখনো তাঁর হুইস্কিপ্রীতি। ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়, তার পরাকাষ্ঠা ছিলেন রাহমানভাই। মৃত্যুভয় নয় , মৃত্যু হবে , এই বেদনা ছিল তাঁর। একবার বলেছিলেন আমাকে `আমি চলে গেলে তাজমহল তো থাকবে। তাতে কী লাভ আমার?'
বেগম সুফিয়া কামাল: এই মহিয়সী নারীর সান্নিধ্যে আসতে পারা আমার জীবনের অন্যতম পরম প্রাপ্তি। তাঁর ধানমন্ডির বাসায় সস্ত্রীক যেতে কী সমাদরের সঙ্গেই না মুহূর্তে আপন করে নিয়েছিলেন আমাদের! কলকাতা থেকে এসেছি বলে কলকাতার হালহকিকত জানতে চাইলেন , এখনো সেখানে ভোরবেলা জল দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার হয় কিনা , নিউ মার্কেটের দোকানপাট নিয়ে কতো জিজ্ঞাসা তাঁর! কলকাতা তো তাঁর ও স্মৃতির শহর!
নিজের লেখা বই উপহার দিলেন আমাদের, 'একালে আমাদের কাল' ও একাত্তরের ডায়েরি।' এ সৌভাগ্যের তুলনা আছে? দেখা হয়েছিল তাঁর বেহান বীণাপাণী দেবীর সঙ্গে সিলেটে। সত্তরোর্ধ মহিলা দেশ - এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিকে মগ্ন। সেখানেই আলাপ হয়েছিল সুফিয়া বেগমের কন্যা লুলু আপা ও তাঁর স্বামী সুপ্রিয়দার সঙ্গে।
বেগম সুফিয়ার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বার্ধক্যেও কিশোরীসুলভ অবলোকন ও দৃষ্টিভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদধন্য তাঁর আশীর্বাদধন্য আমি, এ কথা যতোই ভাবি, উৎফুল্ল না হয়ে পারি না।
আনিসুজ্জামান: আমার প্রাত: স্মরণীয়দের একজন। আমাকে যে কতোভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন! একবার তাঁকে কোচবিহারের দিনহাটায় আন্তর্জাতিক সাহিত্যসভায় নিয়ে যেতে চাইলাম। স্বভাবসুলভ রসিকতায় জানতে চাইলেন , ওখানে গোরস্তান আছে তো! গিয়েছিলেন। সেটা2015. তাঁর বয়স এবং শরীরের বিবেচনায় সেখানে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে সাতসমুদ্র তের নদী পেরোনোর চেয়েও অধিক। তবু আমার প্রতি অসীম স্নেহবশত গিয়েছিলেন। একটিমাত্র ইচ্ছে ছিল তাঁর। তাঁকে যেন সঙ্গীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীনের বলরামপুরস্থিত বাড়িটি দেখানোর ব্যবস্থা করি। তাঁর সেই ইচ্ছে পূরণ করতে পেরেছিলাম।
তাঁর পত্রিকা 'কালি ও কলম ' এ আমার প্রচুর লেখা ছেপেছেন তিনি। তিনি কলকাতা এলেই দেখা করতাম, আর ঢাকা গেলে তো কথা- ই নেই। প্রথম যেবার তাঁর গুলশানের বাসায় যাই, পথনির্দেশ জানতে চেয়েছিলাম। গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন! মহত্ত্ব কাকে বলে , তা তাঁর কাছ থেকে শিখেছি।
২০০০ সাল পর্যন্ত লিখেছেন তিন খণ্ড আত্মজীবনী। তাঁকে বলেছিলাম পরবর্তী ঘটনা লিখতে। বললেন, মন:সংযোগ থাকছে না। সেটা ২০১৭ আমি বলেছিলাম, আপনি মুখেমুখে বলবেন , আমি অনুলিখন করবো। দুদফায় করলাম - ও। কিন্তু পরে আর সময় বের করতে পারেন নি। কাজটা অসম্পূর্ণ-ই রয়ে গেল।
আরো একটি কাজ তাঁর সঙ্গে করবো ভেবেছিলাম। উনি রাজিও হয়েছিলেন। ফাদার দ্যতিয়েন - সম্পাদিত 'গদ্যপরম্পরা' বইটি বের করা। উনি ভূমিকা লিখবেন। আমার কাছেবইটির একটি কপি ছিল, দিয়েছিলাম। উনি পড়ে বললেন, নি: সন্দেহে মূল্যবান সঙ্কলন। কিন্তু তিনি বিশদ লিখতে পারবেন না, বইটির সামান্য পরিচায়িকা লিখে দেবেন। বিস্তৃত ভূমিকা আমাকে লিখতে বললেন। হলো না সে কাজটিও। করোনায় চলে গেলেন তিনি। আমার ওপরে যে তাঁর আস্থা ছিল, এই কথা ভেবে আবেগায়িত , আপ্লুত হই।
হাসান আজিজুল হক: তাঁর সঙ্গে কলকাতায় আলাপ হয় যখন, তাঁর লেখা বিশেষ পড়া হয়নি। একমাত্র 'এক্ষণ ' পত্রিকায় তাঁর একটি গল্প পড়েছিলাম, ' জীবন ঘষে আগুন '। ১৯৮৯- তে রাজশাহীতে গেলাম যখন , সেই সামান্য পরিচয়ের সূত্রে তিনি এক সপ্তাহকাল আমাকে, আমার স্ত্রীকে তাঁর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে আতিথ্য দিলেন। সে দিনগুলো সোনা নয় , হীরে দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো। আমাদের জ্ন্য রাজকীয় বাজার করা আর জোর করে করে খাওয়ানো , বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আড্ডায় আমাদের সামিল করা ও সেই সূত্রে আলী আনোয়ার , সারওয়ার জাহান , জুলফিকার মতিন , সনৎকুমার সাহা প্রমুখ অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে অবিরাম রঙ্গরসিকতায় রাজশাহীর দিনগুলি রাতগুলিকে ভরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সেই সাথে হাসানজায়ার সদা হাস্যময় মুখ , অপূর্ব রান্না পরিবেশন , হাসান ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হৈ হট্টগোল , কী যে অন্তরঙ্গতাভরা সময় কেটেছিল , তা ভাবলে দীর্ঘদিন পরেও স্মৃতিতাড়িত হই , মনে পড়ে কবি কীটস - এর অব্যয় চরণ , ' A thing of beauty is a joy for ever '! পরে হাসান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে বহুবার। তাঁর ' আনন্দ পুরস্কার ' পাওয়া প্রত্যক্ষ করেছি ,ঢাকা রাজশাহী বগুড়ায় সাহিত্যসভায় দেখা হয়েছে। পরে ওঁর মেয়ে সুমন যখন কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছিল সুবিনয় রায় এবং গীতা ঘটকের কাছে , তখন হাসান ভাইয়ের নির্দেশে আমি সুমনের লোকাল গার্জেন ছিলাম। ওঁর ' আগুনপাখি '- র সমালোচনা লিখেছিলাম ' শব্দঘর '- এ। পড়ে বলেছিলেন , ' আমার রচনাবলী নতুন করে খণ্ডে খণ্ডে বেরোচ্ছে। তোমাকে দেবো। তুমি আলোচনা করবে।' প্রথম খণ্ড বেরোবার আগেই চলে গেলেন তিনি!
নাজিম মাহমুদ: হাসান - নাজিম হরিহরাত্মা। প্রথমজন রাজশাহীতে দর্শনের অধ্যাপক , আর অন্যজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার। তাছাড়া নাজিমভাই কবি , গীতিকার , আবৃত্তিকার ও বাংলাদেশের বিখ্যাত সংস্কৃতিজন। বাংলাদেশের প্রথমতম আবৃত্তিসংস্থা ' স্বনন ' তাঁর হাত দিয়েই জন্মলাভ করে। একসময় খুলনার কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। খুলনায় যে সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ' সন্দীপন ' নামে , সেখানে হাসানভাই , সাধন সরকার , আবু বকর সিদ্দিকী , নগেন্দ্র দাশদের মতো তিনিও যুক্ত ছিলেন।
১৯৮৯-তে তাঁর সাথে আলাপ , যদিও খুলনা থেকে কলকাতা এসে আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন যে নগেনস্যার , তাঁর মুখে বহু কথা শুনেছি তাঁর সম্পর্কে।
তিনি এলেন কলকাতায়। একদা এ শহরে তিনি খোদ রাজভবনে ছিলেন , তাঁর বাবা পাকিস্তান আমলে স্পিকার থাকার সুবাদে। এবার তিনি এই অধমের বাসায় অতিথি। তাঁকে আমাদের বাড়িতে আতিথ্য দেবার সাহস পেয়েছিলাম তাঁর সারল্য ও সহজ জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল বলে। সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ওঁর। খুলনায় স্কুলে সহপাঠী ছিলেন ওঁরা। শ্যামলদার সঙ্গে আলাপ ছিল আমার। তাঁকে ফোন করতেই ' আলো কলকাতায় এসেছে ' - বলে চীৎকার।' কাল-ই নিয়ে এসো।
নিয়ে গেলাম নাজিম ভাইকে শ্যামলদার আনোয়ার শাহ্ রোডের বাসায়। আমাদের সঙ্গে গেল হাসান ভাইয়ের মেয়ে সুমন।সারাদিন প্রাণ খুলে আড্ডা , খাওয়াদাওয়া , বিকেলে কলেজস্ট্রিট নিয়ে গিয়ে শ্যামলদার বই নাজিভাইকে উপহার দেওয়া। পরদিন শান্তিনিকেতনে। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁর পরিচিত। যাওয়ামাত্র আপ্যায়ন! এসবের সাক্ষী হওয়াও সৌভাগ্যের।
প্রায় একমাস আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আবৃত্তিকার ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। একবার তাঁকে ডাকা হলো। ব্রততী - নাজিম কবিতাসন্ধ্যাটি অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো। সেদিন আমার আবৃত্তিকার বন্ধু দীপঙ্কর আর নতুন প্রজন্মের আবৃত্তিশিল্পী সেলিম দুরানীও ছিল। নাজিম ভাইকে ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠান করে বাংলা একাডেমি মঞ্চে সম্বর্ধনা দেবার ব্যবস্থা করতে পেরে কৃতার্থ বোধ করি আজ -ও।
এসেছিলেন আসলে চিকিৎসা করাতে। লিভারে ক্যানসার ধরা পড়লো। অন্তিম পর্যায়ে! ঢাকায় ফিরে গিয়ে দ - তিন মাসের মধ্যে মারা গেলেন। বলেছিলেন , আমাকে নিয়ে সুন্দরবন বেড়াবেন। চিঠি লিখতে ভালোবাসতেন। আমাকে লেখা তাঁর চিঠিগুলো আমার কাছে অক্ষয় সম্পদ।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: ইলিয়াস ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ ১৯৮৫- তে , নারিন্দায় তাঁর বাসায়। প্রথম আলাপেই তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে গেলেন। উনি বিরতিহীন ছিলেন আড্ডায়। মনে হতো আড্ডা ছাড়া উনি আর কিছুই করেন না। কলেজে পড়ানো, লেখালেখি , দেশিবিদেশি গ্রন্থপাঠ, বিভিন্ন জায়গায় আমন্ত্রিত বক্তা হিশেবে যাওয়া , সংসারজীবনের দায়িত্ব সামলানো, এসব তিনি করতেন কখন? অথচ করতেন। তিনি যতোটা বোহেমিয়ান , দীর্ঘ পরিচয়ে দেখেছি , ততোটাই গৃহপালিত।
পাইপ টানতেন। কথা শোনার চেয়ে বলাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল , আর বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যেতেন দ্রুত। রসিকতাবোধ ছিল অসম্ভব রকমের। নিজেকে নিয়েও রসিকতা করতে ছাড়তেন না। কলকাতায় যেবার ক্যানসারের জন্য পা বাদ দিতে হলো , পার্কসার্কাসে তাঁর আত্মীয়র বাসায় দেখা করতে যেতে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন ,' এখন আমি আখতারুজ্জামান লঙ '। তৈমুর লঙ খোঁড়া ছিলেন , সেই অনুষঙ্গে।
আবার এক - ই সঙ্গে তাঁর সৌজন্যবোধ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। রিপোজ নার্সিংহোমে তিনি তখন ভর্তি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় - ও অসুস্থ হয়ে সেখানে ভর্তি। আমার হাত দিয়ে তাঁকে ফুল ও চিঠি পাঠালেন।
একবার কলকাতায় গেছেন। আমাকে বললেন , বাঙ্গালকে হাইকোর্ট চেনাতে হয় না , এই বিখ্যাত প্রবাদটি তাঁর ক্ষেত্রে সত্য নয়। আমি কি তাঁকে একবার কলকাতা হাইকোর্ট দেখাতে নিয়ে যেতে পারি? নিতান্তই রসিকতা করে বলা।
তাঁর সঙ্গে আমার যে স্মৃতি , তা নিয়ে মহাভারত লেখা যায়। তিনি ও সুরাইয়াভাবী , তাঁদের ছেলে পার্থ , তিনজনকেই খুব মনে পড়ে। সেদিনের সেই পার্থ আজ কলকাতায় বাংলাদেশ সরকারের ডেপুটি হাই কমিশনার! কী যে উৎফুল্ল হওয়ার মতো সংবাদ!
ইলিয়াসভাইয়ের চিলেকোঠা আর খোয়াবনামা নিয়ে আলোচনা আছে আমার। তাঁর প্রথম গল্প ' নিরুদ্দেশযাত্রা ' নিয়েও প্রবন্ধ লিখেছিলাম।
আল মাহমুদ।। তাঁকে নিয়ে লিখবো কী , তিনি - আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখে বসে আছেন ! ' কবির আত্মবিশ্বাস ' বলে যে প্রবন্ধের বই আছে তাঁর , সে বইতে ' কলকাতার মুগ্ধ দম্পতি ' নামে সে লেখাটি আমাকে নিয়ত লজ্জায় ফেলে এ - জন্য ই , আমার মতো একজন নগণ্য মানুষকে নিয়ে ' সোনালী কাবিন '- এর কবি লিখলেন ! আসলে মাহমুদভাই আজানুলম্বিত সরল মানুষ , পরিচয়ে জেনেছি। যাকে ভালোবাসেন , মাত্রাতিরিক্ত গভীরতা দিয়ে বাসেন। আমাদের প্রতি অগাধ স্নেহ - ই তাঁকে দিয়ে লেখাটি লিখিয়েছিল।
জীবিতকালে এবং এখনো তিনি বিতর্কিত। তিনি তাঁর বেদনার কথা বিস্তারিত বলেছিলেন আমাকে। সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে জেলে গেলেন যখন , বাহবা দিয়েছিলেন অনেক বুধজন , কিন্তু তাঁর অভুক্ত পরিবারকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে দেখা যায় নি কাউকে। পরে তারাই সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন তাঁকে। উপমহাদেশে তাঁর মতো কবি কজন ? জীবনানন্দ - পরবর্তীকালে প্রথম উচ্চার্য কবির নাম আল মাহমুদ। তাছাড়া তাঁর গল্প ও উপন্যাসসমূহের - ও বাংলাসাহিত্যে একটি সম্ভ্রান্ত স্থান আছে। একজন ভক্ত মুসলমান ছিলেন তিনি। তার পাশাপাশি হিন্দু বৌদ্ধ কনফুসীয় ধর্ম নিয়ে তাঁর নিবিড় পড়াশোনার যে পরিচয় পেয়েছি , তাতে মনে হয়েছে , মানুষটি অসম্ভবরকমে ধর্মজিজ্ঞাসু।
বেলাল মোহাম্মদ: মানুষটি ঈশ্বরকোটির। অকালে স্ত্রী ও পুত্রহারা। তাঁর মতো আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষ খুব বেশি দেখিনি। একাত্তরের ক্রান্তিলগ্নে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি এবং থাকবেন চিরকাল।
চট্টগ্রামে তিনি ' স্বাধীন বাংলা বিদ্রোহী বেতার কেন্দ্র ' গড়ে তুলেছিলেন। কালুরঘাটে। ছাব্বিশে মার্চ তাঁর হাতে আসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা - ঘোষণাপত্র। সেটি অবলম্বন করে তিনি দ্রুত একটি স্ক্রিপ্ট লেখেন , এবং তা জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে প্রচারিত হয়। একাত্তরের ঐ দুরূহ সময়ে এঁর সঙ্গে আলাপ হতে জেনেছিলাম, আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে রামায়ণ - মহাভারত উপহার দিতেন। চাইতেন , এই দুটি মহাকাব্যের সঙ্গে নতুন প্রজন্ম পরিচিত হোক। কবিতা লিখতেন , প্রবন্ধ - ও। বাংলা একাডেমি ও স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন তিনি।
অমায়িক ও শান্তস্বভাবের বেলালভাই তাঁর খ্যাতির জোরে আখের গোছাতে পারতেন ভালোই। কিন্তু সে - পথে হাঁটেন নি কখনো। কলকাতায় এলে খুব শস্তা হোটেলে থাকতে দেখে একবার আমাদের বাসায় ধরে নিয়ে এসেছিলাম।
অফুরান গল্পের ভাণ্ডার তাঁর। দেশের জন্য ভালোবাসার স্থায়ী চিহ্ন ফুটে উঠতো তাঁর কথাবার্তায়। খুব বেশি পাইনি তাঁর সান্নিধ্য। যতোটুকু পেয়েছি , তাতে ওঁকে নমস্য বলে মেনেছি , বিশেষ করে যখন শুনলাম , তিনি মরণোত্তর দেহদান করে গিয়েছিলেন।
বেলাল চৌধুরী: বাংলাদেশে আমার যাবতীয় পরিচিতজনের মধ্যমণি বেলালদা। আর কেবল আমার - ই নন , আমার মতো অজস্র লোকের। জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশের , কিন্তু এই একজন ব্যক্তি , যাঁর ঠাঁই ভারত - বাংলাদেশ জুড়ে। প্রথমজীবনে ঘর ছেড়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে উপনীত হন কলকাতায়। কৃত্তিবাসগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় হয়। বছরের পর বছর কাটিয়ে পরে একাত্তরে ফের ঢাকা। কলকাতায় এক পা , ঢাকায় অন্য পা ছিল তাঁর আমৃত্যু। সেজন্যই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর শামসুর রাহমান সমান নিকটজন তাঁর , সৈয়দ শামসুল হক এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অনুজদের কাছে তিনি ছিলেন মুশকিল আসান। যতোবার ঢাকায় এসেছি , অভিভাবকের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। মনে আছে , 1985-তে যেবার ঢাকা আসি , আমাকে নিয়ে গেলেন বুড়িগঙ্গা নদীর নৌ - হোটেলে। ওখানে নৌকোয় বসে পাঁচমিশেলি মাছের ঝোলের স্বাদ গ্রহণ করালেন। টাকা ভাঙাতে হবে , মুহূর্তে করে দিলেন। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হবে , হয়ে গেল অনায়াসে। নির্মলেন্দু গুণের ' হুলিয়া ' কবিতা অবলম্বনে তানভীর মোকাম্মেলের প্রথম ছবি দেখেছিলাম ওঁর বদান্যতায়। পরে আমার পত্রিকায় লেখা চাইলে ভিয়েতনাম নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের না - হওয়া ছবি নিয়ে লিখলেন। ওঁর মাধ্যমেই আলাপ হয়েছিল শামসুর রাহমান , হুমায়ূন আহমেদ , খসরুভাই , রবিউল হুসাইন , ইমদাদুল হক মিলন ও আরো বহু কবি - লেখকদের সঙ্গে। যেবার আমার স্ত্রী দেবাঞ্জলিকে নিয়ে ঢাকায় এলাম , ওঁর সম্পাদিত পত্রিকা ' ভারত বিচিত্রা '- য় কবিতা ছাপলেন ওর। প্রসঙ্গত , দেবাঞ্জলির দিদি কবি দেবারতি মিত্র বেলালভাইয়ের সুপরিচিত বিধায় দেবাঞ্জলিকে নিয়ে কী যে করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। একবার আমাদের দামি রেস্তোঁরায় লাঞ্চ খাওয়ান , আমাদের ঢাকা ঘুরিয়ে দেখান , ওঁর পত্রিকা - অফিসে গেলে আলাপ করিয়ে দেন ওগানে আসা গুণী মানুষদের সঙ্গে।
কলকাতায় প্রায় - ই আসতেন। কখনো হোটেলে , কখনো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে উঠতেন। সুনীলদা - স্বাতীদি হয়তো বেড়াতে গেছেন , ঘরে বেলালদাকে রেখে।এই সখ্য বড়ো বিরল , যা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এবং সেখানে বসে দীর্ঘ আড্ডা , আড্ডা - অন্তে মধ্যাহ্নভোজ , বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতিকে তোয়াক্কা না করে ! অবিশ্বাস্য সে - সব দিন!
সুনীলদা প্রয়াত হলে বেলালদার অন্য আর এক মূর্তি দেখেছি। সুনীলদার অন্ত্যেষ্টি হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর দুই কি তিনদিন পরে , ছেলে সৌভিক আমেরিকা থেকে আসবে , সেজন্য। অন্ত্যষ্টির দিন শ্মশানে গিয়ে দেখি , বেলালদা পাগোলের মতো , আক্ষরিখ অর্থেই পাগোলের মতো শ্মশানময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর হাতে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একগাদা দৈনিক পত্রিকা , যা বেরিয়েছিল সুনীলদার মৃত্যুর পরদিন। উনি নিয়ে এসেছিলেন। প্রতিটি কাগজ সুনীলদার ওপর বিশদ লেখা ছেপেছে।সেদিন বেলালদাকে দেখে মনে হয়েছিল , আত্মীয়বিয়োগের দু:খ কী তীব্র , কী মর্মঘাতী , এবং তা কতোখানি আমূল রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে!
বেলালদাকে নিয়ে কথার শেষ নেই। রয়ে গেছে একটি বেদনা , অপরাধবোধ। তিনি যখন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে , ঢাকায় ছিলাম , তবু দেখা করতে যেতে পারিনি। বেলালদা , ক্ষমা করে দিন।
পরে , এই তো মাস ছ - সাত আগে , বেলালদা সম্পর্কে জানতে চাইলেন রংপুরের কবি শাহাদাত দিলরুবা। বললাম , বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে তুমি তাঁর সম্পর্কে জানো না? বললাম। পরে শুনলাম , দিলরুবার মেয়ের সঙ্গে আমেরিকাবাসী বেলালদার ছেলের বিয়ে হয়েছে।প্রতীকের সঙ্গে কি? শাহাদাতের মেয়েকে চিনি। কম্পিউটার নিয়ে আমেরিকায় পড়ে। চমৎকার ছবি আঁকার হাত।
বেলালদাকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করে তাঁর ছেলে প্রতীক ' প্রথম আলো '- তে যা লিখেছেন , সেটা উদ্ধৃত না করে পারছি না। ' এক আশ্চর্যরকম বৈচিত্রে্যর অধিকারী কবি বেলাল চৌধুরী ত্তাঁর জ্ঞান , সুমধুর ভাষার ব্যবহার ও হৃদয়ের প্রশস্ততা দিয়ে জয় করে নিয়েছিলেন দেশবিদেশের খ্যাতিমান নক্ষত্রপুঞ্জের মন , তেমনি সরল ভালোবাসার আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন কাঁচাবাজারের সবজিবিক্রেতা সুলতান মিঞা থেকে শুরু করে পুরানা পল্টনের সেগুনবাগিচা এলাকার পুরাতন বইয়ের ব্যবসায়ী বাচ্চু মিঞার মতো অতি সাধারণ মানুষদের। ' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে বেলালদার ছবি সুন্দর চিত্রিত করে গেছেন। বেলালদাকে নিয়ে কবিতা তো বটেই , গল্প - উপন্যাস পর্যন্ত লেখা হয়েছে। তিনি নিজে কবিতা ছাড়াও অনুবাদ করেছেন প্রচুর , লিখেছেন আত্মজীবনী। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি ও একুশে পদক। বেলালদাবিহীন ঢাকা আমার কাছে অনেকটাই বিবর্ণ, পানসে !
ওয়াহিদুল হক: তাঁর সঙ্গে মাত্র একদিনের মোলাকাত , কিন্তু সেই পরিচয় , সমস্ত দিন ও রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যলাভ আমার জীবনে এক আগ্নেয় সঞ্চয়। মানুষটি সম্পর্কে জানতাম বহু আগে থেকেই। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞান , সনজীদা - সহযোগে ছায়ানট স্থাপনা , বৈদগ্ধ্যপূর্ণ লেখনীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু মানুষটির মধ্যে যে সহজতা , এতো বিশাল মাপের মানুষ হয়েও সবার সঙ্গে অকপট ও দ্বিধাহীন মিশতে পারা , এসব অভিজ্ঞতা ওই একটি দিনেই হয়েছিল। সেদিন উনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন যাঁদের বাসায় ( গান শেখাতে গিয়েছিলেন। লেজুড় হিশেবে সঙ্গে ছিলাম ) , তাঁরা দুজনেই খ্যাতিমান , - ইফফাত আরা এবং শামা রহমান। সন্ধ্যায় আমি তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলাম আমি সিদ্ধেশ্বরীতে যার বাসায় থাকি সেখানে। বিন্দুমাত্র আপত্তি না করে তিনি সেখানে তো গেলেন - ই , গানে গল্পে মাতিয়ে রাখলেন সবাইকে। রাতে আহার করতে বলায় নির্দ্বিধায় রাজি হলেন। উপনিষদে পড়েছিলাম , যিনি নিজের মধ্যে অপরকে এবং অপরের মধ্যে নিজেকে দেখতে পান , তাঁর দেখাটাই প্রকৃত দেখা। ওয়াহিদুলভাই তার মূর্ত প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন আমার কাছে। অহংবর্জিত আপাদমস্তক একজন সজ্জন মানুষ , নিজেকে যিনি রবীন্দ্রনাথের সন্তানস্বরূপ ভাবতেন , বলে গিয়েছিলেন তাঁর মরদেহ ঘিরে যেন ' আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে ' গাওয়া হয়। মরদেহ দান - ও করে গিয়েছেন এ - যুগের এই দধীচী। গান , আবৃত্তির জগতে থেকেও পঞ্চাশ বছরের ওপর সাংবাদিকতা করেছেন একাধিক ইংরেজি দৈনিকে। স্থাপত্যবিদ্যার অধ্যাপনাও করেছেন একুশে ও স্বাধীনতা পদক পাওয়া এই শ্রদ্ধেয় মানুষটি।
সেলিম আল দীন: এক দীপ্র প্রতিভার নাম। বাংলা নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথের পরে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন যুগন্ধর নাট্যব্যক্তিত্ব জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম তিনি। উৎপল দত্ত মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে তুলনীয়। তবে উৎপল নাটক লেখার পাশাপাশি অভিনয়ও করতেন। ছিলেন নাট্যপরিচালক। সেলিমের প্রতিভা কেন্দ্রীভূত ছিল নাটক লেখা ও মূলত নাট্যবিষয়ক গবেষণাকাজে। সৈয়দ শামসুল হককে এই কাতারে রাখতেই হবে। তবে তিনি নাটকে মনোযোগী ছিলেন তুলনায় কম।
নাট্যরচনা তো আছেই। সেলিম অভিনন্দিত হয়ে থাকবেন বাংলা নাটক নিয়ে তাঁর একক ও অকৃত্রিম চিন্তাভাবনা নিয়ে। আধূনিক বাংলা নাটক ঔপনিবেশিক লেবাসে আবির্ভূত হয়েছে এতাবৎকাল। বাংলার নাট্য ঐতিহ্য যে দীর্ঘদিনের এবং তা সহস্রবছরের আবর্তনে আমাদের এই বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে বাংলা নাটকের প্রকৃত বিবর্তনবাদের ডারউইন হয়ে থাকবেন তিনি।
তাঁর সঙ্গে কলকাতা ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার আলাপ ও মতবিনিময় হয়েছে। মৌলিক চিন্তা যে কতিপয় মানুষের পরিচয়চিহ্ন তিনি তাঁদের অগ্রগণ্য।
আনোয়ারাদি: দু হাজার আট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষে তাঁকে নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করেছে। বু. ব. সেখানে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগের উদ্গাতা ছিলেন।সেমিনার উপলক্ষ্যে এসেছেন কেতকী কুশারী ডাইসন , সৈয়দ শামসুল হক - সহ আরো অনেকে। সৈয়দ হককে আগেই চিনতাম। এবার আলাপ হলো তাঁর স্ত্রী আনোয়ারা সৈয়দ হকের সঙ্গে। পেশায় চিকিৎসক আনোয়ারার গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ শিশুতোষ রচনা , - সর্বত্রই পদচারণা। আলাপ হলো। কিন্তু তা নিতান্তই ক্ষীণ।
এরপর সৈয়দ হকের মৃত্যু। কলকাতা বইমেলায় এলেন আনোয়ারা। দেখা হলো। কথা হতে পেরেছিল সামান্যই। সেটা হলো 2018- তে ঢাকায় এলাম যখন। আলাপ , অন্তরঙ্গতা। কতো বিষয় নিয়েই না কথা বলেছি আমরা তাঁর গুলশানের বাসায় , বারডেম হাসপাতালে তাঁর চেম্বারে , স্টার পত্রিকার ক্যনটিনে। ততোদিনে তিনি আমার আনোয়ারাদি হয়ে গেছেন। ক্যানটিনে ঢুকেই বলেন নানী, মাসুদের ফুফু , জিন্নাভাইয়ের মা।। সাধারণে অসাধারণ এঁরা। প্রথমে বলি নানীর কথা।
তিনি মোটেই নানীবয়সিনী নন। চাকরি করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ইনস্টিটিউশনে। আমার বন্ধু কবি বিমল গুহর মাধ্যমে আলাপ। অসম্ভব হাসিখুশি সবসময়। মাঝেমাঝেই আড্ডা দিতে যেতাম। ওঁদের অফিসে। জেনেছিলাম শেরে বাংলার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতেন। একবার তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখি, খিচুড়ি আর ইলিশের ফিস্ট জমে উঠেছে। আমাকে পেয়ে নানীর কী আনন্দ ! কষে ইলিশ খাওয়ালেন।
সেবার সস্ত্রীক ঢাকা গিয়ে বিমলের যাত্রাবাড়ির ডেরায় উঠেছি। আমাদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। গল্প , গল্প আর গল্প। আর কথা বলতে বলতে হাসিতে গড়িয়ে পড়া। সেদিন নানীর মা ছিলেন। ধবধবে ফরসা , পানে - জর্দায় মুখটি রঙিন , এবং হাসিরাশি সেই মুখে। নানীর হাসার কথা ছিল না , এতো বিধুর ও গভীর ক্ষত তাঁর বুকে। বলেছিলেন আমার স্ত্রীকে।
ফেরার পথে রিকশায় তুলে দিতে গিয়ে খুব দ্রুত রিকশাচালককে ভাড়াটা দিয়ে দিলেন। সৌজন্যবোধ! 'উদিত দু:খের দেশ ' - এর কবি মাসুদ যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিল , তখন আলাপ আমার সঙ্গে। আমি বাংলাদেশে যাবো , সে একেবারে বেনাপোল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। বিদায় নেবার সময় মাসুদ বললো , যশোরে যেন ওর পিসির বাসায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে ঢাকায় যাই।ভাবলাম , সেটাই ভালো হবে। পিসির বাড়ি গিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়লাম। পিসির পাঁচ মেয়ে। দুই ছেলের একজন কলকাতায়। শাশুড়ি আছেন। স্বামী নড়াইলে ওকালতি করেন , সপ্তাহান্তে বাড়ি আসেন। অতএব সাতজন বিভিন্ন বয়সের নারী , যাদের অধিকাংশ - ই তরুণী , অসোয়াস্তি হবে না? রাতে ঘুমোবার সময় ভেবে রাখলাম , কাল ভোর নাহতেই -----
কিন্তু বিধি বাম। মাঝরাতে কান্না , আর তা উত্তরোত্তর বাড়ছিলো। দরজা খুলে যে দেখবো , সঙ্কোচবশত পারা যাচ্ছিলো না। আলো ফুটতে দরজা খুলে ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখি , জনা পনেরো মানুষের সমবেত কান্না। পিসি সামলাতে চেষ্টা করছেন, পারছেন না।
ধীরে ধীরে ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। ফুফুর এক বোনপো নীলফামারীতে থাকতো। পুকুরে ডাইভ দিতে গিয়ে তীব্র আঘাতপায় বুকে, এবং বুক থেখে নিম্নাংশ অসাড় হয়ে যায়। তাকে শোর এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ঢাকায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালে সুফল মিলতেও পারে। কান্না অসুস্থ যুবকের মা , ভাইবোনদের। যাবতীয় ব্যবস্থা করা হলো ফ্লা ঢাকা নেবার। মাসুদের পিসি - ও যাবেন। পিসি আমাকে অনুরোধ করলেন , যতোদিন ফিরে না আসেন, আমি যেন থাকি। হাটবাজারের টাকা দিয়ে গেলেন।
আমি না বলার ফুরসত পেলাম না। ফিসির ছেলে আছে বটে , তবে সে পনেরো - ষোলো বছরের কিশোর। এর দ্বারা বাজারটাজার সম্ভব না। আমি কেবল ভাবছিলাম , মুসলমানরা সাধারণত রক্ষণশীল হন ( পিসির শাশুড়ি , সত্তরের ওপর বয়স , আমার সামনে একহাত ঘোমটা না দিয়ে আসতেন না )। সেখানে একদিনের - ও কম সময়ের পরিচিত আমাকে দায়িত্ব দিচ্ছেন তাঁর চৌদ্দ , আঠারো , উনিশ , বাইশ আর তিরিশ বছর বয়সী মেয়েদের অভিভাবকত্বের ( বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী বিদেশে বলে সে তখন পিতৃগৃহে ) ! আর আমিও তো পঁয়তিরিশের!
দু সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল। পিসি ফিরে এলেন , রোগীর অবস্থা ভালোর দিকে জানালেন। বাজারহাট কেমন করেছি জানতে চাইলেন। আচ্ছা, একজন অতিথির ওপর যদি মেজবানের বাড়ির বাজারসরকার করা হয় , তাহলে কি তার প্রাণখুলে বাজার করা সম্ভব? হতো - ও তাই। ইলিশমাছ আনতাম প্রায়শ , কেননা তখন সেটাই ছিল শস্তার মাছ , পনেরো - বিশ টাকা করে ( 1985- সালের কথা বলছি। তখনো ইলিশ কৌলিন্য বজায় রেখে চলতো , তাকে দাঁড়িপাল্লায় ওঠানোর ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস পায়নি কেউ )।
পিসি দেখলাম অস্বস্তিতে। উনি এসেছেন, আমি দায়মুক্ত হয়ে বিদায় নিতে চাইলাম। পিসি যেতে দিলেন না। আমাকে পরিপাটি করে না খাইয়ে ছাড়বেন না। মাঝখানে নড়াইল থেকে পিসির বর, অর্থাৎ মাসুদের সূত্রে আমার-ও ফুপা , এসেছিলেন। আমি তাঁকে দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি বললেন , ওসব হবে না। আমি তো এ - বাড়িতে সপ্তাহান্তের মেহমান ! কী আর করা!
পরবর্তী দু - তিন দিন পিসির আওতায় থেকে চর্ব্যচুষ্য খাওয়া গেল। তাঁ র হাতের রান্না খেয়ে মনে হচ্ছিল , বাকি জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দিলে হয় না? হল না বলেই পরে জিন্নাহ্ ভাইয়ের মায়ের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সে এক মজার অভিজ্ঞতা। তার আগে পিসিবৃত্তান্তের শেষাংশ। রোজ - ই গল্প হতো পিসির সঙ্গে। একদিন কথায় কথায় পিসি বললেন , তোমাদের (হিন্দুদের ) সব -ই ভালো। কিন্তু একটা জিনিশ খুব খারাপ লাগে আমার , - তোমরা মৃতদেহকে পুড়িয়ে ফেলো। আমিও উত্তর দিতে ছাড়লাম না , - আপনাদের - ও সব ভালো। কেবল একটা জিনিশ বাদে। আপনারা মৃতদেহ মাটিচাপা দেন। দম বন্ধ হয় না তাতে? এরকম - ই নির্দোষ মজা করেছি দুজনে।
জিন্নাহ্ভাইয়ের পর্ব ঢের পরের। ১৯৯৭- এর। ঢাকায় আমার ভগ্নীস্থানীয়া শিরীন আপার বাড়ি উঠেছি। শিরীনের শাশুড়ি দেখলাম প্রথম দিন খানিক অস্বস্তিতে। পরদিন শিরীন আপা বললো , তুমি পাশ। কীসের পাশ,? শিরীন: শাশুড়ি জানতে চেয়েছেন, আমি কি ব্রাহ্মণ হিন্দু? যেই শুনলেন সদর্থক উত্তর , অমনি তাঁদের বাসায় আমার অবস্থান নিষ্কণ্টক হয়ে গেল।
মজা আরো আছে। রোজ সক্কালবেলা শিরীন ও জিন্নাহ্ভাই কাজে বেরিয়ে যেতেন। আমি আর শাশুড়ি পাশাপাশি বসে নাস্তা করতাম। সকালে গুরুভার আহার করতাম না। রুটি আলুভাজি , ব্যস। আর উনি পরোটা আর গোমাংস নিয়ে বসতেন। আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা এবং তারিফযোগ্য। ছোটবেলা থেকে দেখেছি , আমার দুই মাসি , পিসি , বেশ কয়েকজন আত্মীয়তাসূত্রে দিদিমা - ঠাকুমাস্থানীয়া আমাদের বাড়ি এলে নিরিমিশ খেতেন। মুসুর ডাল নিষিদ্ধ , চপ সিঙ্গারা নিষিদ্ধ , পেঁয়াজের তো প্রশ্ন - ই নেই। ছিল একাদশী-সহ নানান উপলক্ষ্যে উপোসের ঘনঘটা।এমন কি রাতে ভাতের বদলে কেবল খই। মুড়ি-চিড়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল তাদের, পুরুষতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে। সেখানে ইনি একেবারে গোরুগোশত! মারহাবা !